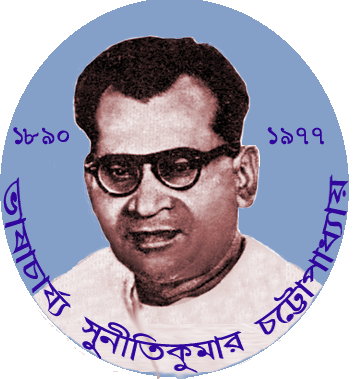অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জীর ১৩২ তম জন্মবার্ষিকী
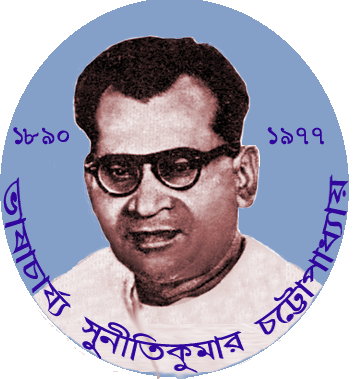
অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য
ভাষা, চিন্তা ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক। উনিশশতকে বাংলাভাষার যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেটির ফলেই এদেশে পাশ্চাত্যের চিন্তুা অতিদ্রুত এদেশের নতুন নগরসভ্যতায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। এর ফলে সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে সমান্তরালভাবে বাংলা ভাষারও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বলা যেতে পারে ১৮০০ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কাঠামোর যে পরিবর্তন তা এদেশে মাতৃভাষাগুলি বিকাশের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করেছিল। যেটি মূলত ফোর্ট উইলিয়ামে রামরাম বসু মৃ্ত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দের হাত ধরে শুরু হলেও রামমোহন ও তৎপরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টিতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগে মানব কেন্দ্রিক একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার কর্মযোগে নিজেদের ব্যাপৃত রেখে। বাংলা ভাষাকে সর্ববিষয়ে সকলের গ্রহণযোগ্য রূপে গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁরা। গার্হস্থ্য জীবনে বাংলার যে রূপ ছিল সেটির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভাষায় পাশ্চাত্যের নতুন নুতন বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটিয়ে ভাষার মর্যাদাকে যেমন বাড়িয়েছিলেন তেমনি ভাষার অঙ্গসজ্জাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় বাংলায় গদ্য উদ্ভবের পরে মাত্র চারপাঁচটি দশকের মধ্যে বিশেষ করে ১৮৪৭এর পর দুটি দশকেই ভাষা তার নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মর্যাদায় ও অঙ্গসজ্জায়। এরই পরিণতিতে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও বঙ্কিমের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। বিশ্বের দরবারে তার অস্তিত্বও প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাকে আজকে সমৃদ্ধ হতে গেলে এবং অন্যান্য মাতৃভাষাগুলিকেও বিকশিত হতে গেলে ভাষা পরিকল্পনায় এই যুগের অবদানগুলি বিবেচনায় আনা প্রাথমিক কর্তব্য।